
আমীন আল রশীদ: ডেইলি স্টার বাংলা থেকে নেওয়া, খ্রিষ্টীয় নতুন বছর শুরুর ২৬ দিন পরে ২৭ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, ইংরেজি নববর্ষ ২০২৫ উপলক্ষে নরেন্দ্র মোদী প্রধান উপদেষ্টাকে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠিয়েছেন। তিনি সেখানে লিখেছেন 'বেস্ট উইশেস ফর দ্য নিউ ইয়ার'।
প্রশ্ন হলো, নতুন বছর শুরুর প্রায় এক মাস পরে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানো কি এক ধরনের তাচ্ছিল্য নাকি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ভারত সরকারের বিলম্বিত উপলব্ধি? এই শুভেচ্ছাবার্তার মধ্য দিয়ে কি দুদেশের সম্পর্কের বরফ গলবে? প্রতিবেশী দুই দেশের সম্পর্ক যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটি আরও পরিষ্কার হলো কি না?
প্রসঙ্গত, গত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। বিভিন্ন ঘটনায় দুই দেশের ক্ষমতাসীনদের প্রতিক্রিয়া উত্তেজনাও ছড়ায়। তবে গত ২৩ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, দিল্লির সঙ্গে ঢাকার দূরত্ব তৈরি হওয়ার বিষয়টি তাকে অনেক কষ্ট দেয়। ড. ইউনূসের এই প্রতিক্রিয়াই কি বিলম্বে হলেও মোদির শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানোয় উৎসাহ দিয়েছে?
মোদি যেদিন বাংলাদেশের সরকার প্রধানকে নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন, সেদিনই তিনি টেলিফোনে কথা বলেছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে। সেখানে তারা দুই দেশের মধ্যকার সহযোগিতা সম্প্রসারণ ও গভীর করার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ আঞ্চলিক অনেক বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের সঙ্গে ড. ইউনূসকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানোর কি কোনো সম্পর্ক আছে নাকি দুটি আলাদা বিষয়? যদিও এই মুহূর্তে দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখারও খুব একটা সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে জনমনে এই প্রশ্নও আছে যে, মোদি কি ড. ইউনূসকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন?
অনেকেই বলাবলি করছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ নেওয়ার পরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাপারে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে এবং ট্রাম্পের সঙ্গে যেহেতু মোদি প্রশাসনের সম্পর্ক ভালো, অতএব বাংলাদেশ প্রশ্নে তারা একটি সমঝোতায় পৌঁছাবেন। টেলিফোন আলাপে কি দুই নেতা সেরকম কোনো সমঝোতায় পৌঁছালেন? যদি তা-ই হয়, তাহলে কী সেই সমঝোতা?
অস্বীকার করা যাবে না, বাংলাদেশ যেহেতু ভূরাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে এর অবস্থান, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের মালিকানাধীন অংশে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা; বাংলাদেশের প্রায় ২০ কোটি মানুষ—যাদের ৯০ শতাংশের বেশি মুসলমান এবং যেখানে ওই অর্থে কোনো জাতিগত বিরোধ বা বিদ্বেষ নেই এবং কিছু বিষয়ে রাজনৈকি বিভক্তি থাকলেও বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু বিশ্বের অনেক দেশের চেয়েই ঐক্যবদ্ধ, কর্মঠ এবং বিপুল জনসংখ্যার যে দেশটি এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের (৫০ শতাংশের বেশি মানুষ কর্মক্ষম) সুবিধার আওতায় রয়েছে—যা অর্থনীতির বিবেচনায় একটি বিরাট শক্তি—সেরকম একটি দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল রাখা যেহেতু প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের এবং দূরবর্তী দেশ হলেও যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ, অতএব এখানে যারাই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা তথা এখানে কোনো ধরনের অস্থিরতা তৈরি হলে সেটি যে আশেপাশের দেশেও, বিশেষ করে ভারতের সেভেন সিস্টার্সকেও প্রভাবিত করবে বলে আশঙ্কা করা হয়—সেই ভয় ও বাস্তবতা মাথায় রেখেই কি বাংলাদেশের ব্যাপারে এখন ভারত নতুন করে চিন্তা করছে? যদি তাই হয়, তাহলে বলতে হবে ২৭ দিনের মাথায় নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর এই সৌজন্যটি 'বেটার লেট দ্যান নেভার'।
বঙ্গোপসাগরের তীরে বাংলাদেশ নামে ছোট্ট দেশটিতে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের নানাবিধ স্বার্থ রয়েছে। তার মানে কি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে এবং তারপরেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকে নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালো দিল্লি? এই শুভেচ্ছাবার্তা কি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিত, যেটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে?
২.
বাংলাদেশ সম্পর্কে আমেরিকা এখন কী ভাবছে? তার দেশের একটি বড় কোম্পানির সঙ্গে সম্প্রতি এলএনজি আমদানির চুক্তি করেছে বাংলাদেশ। সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বৈঠকে ড. ইউনূসের উপস্থিতির সময়ে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানাভিত্তিক আর্জেন্ট এলএনজি কোম্পানির সঙ্গে একটি বড় চুক্তি হয়, যার আওতায় প্রতি বছর ৫০ লাখ টন (৫ মিলিয়ন টন) এলএনজি কিনবে বাংলাদেশ।
গভীর সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে মার্কিন কোম্পানির আগ্রহের কথা বেশ পুরোনো। সেন্টমার্টিন দ্বীপ সমুদ্রের ১১ নম্বর ব্লকে পড়েছে বলে সরকার ওই এলাকাটি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখতে চায়—এমন কথাও বাতাসে ভেসে বেড়ায়। তার কিছু লক্ষ্মণও দেখা যায়।
জুলাই অভ্যুত্থানের আগে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস—যিনি ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে গত ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশে এসেছিলেন নতুন পরিচয়ে। সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি এখন মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জির স্ট্র্যাটেজিক উপদেষ্টা। বাংলাদেশে এলএনজি সরবরাহ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বাড়াতে আগ্রহ দেখিয়েছে এই কোম্পানিটি। এ বিষয়ে পিটার হাস বৈঠক করেছেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের সঙ্গে। এর আগে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি শেভরনও স্থলভাগের পর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।
২০১৪ সালে গণমাধ্যমের একটি খবরে বলা হয়, গভীর সমুদ্রে ১০ ও ১১ নম্বর ব্লকে গ্যাসের আধার (কাঠামো) পেয়েছে মার্কিন কোম্পানি কনোকো ফিলিপস। ধারণা করা হচ্ছে সেখানে পাঁচ থেকে সাত ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ থাকতে পারে। দ্বিমাত্রিক জরিপ শেষে এই ধরণার কথা বলা হয়। ২০১১ সালের ১৬ জুন সাগরের ১০ ও ১১ নম্বর ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য কনোকো ফিলিপসের সঙ্গে উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি (পিএসসি) করে পেট্রোবাংলা। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ২৮০ কিলোমিটার দূরে এই ব্লকের অবস্থান।
বলা হয়, দিন শেষে সবই যেহেতু ব্যবসার খেলা এবং গণতন্ত্র-মানবাধিকারেরর বুলির আড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে মূলত তার ব্যবসা ও বৈশ্বিক আধিপত্য বিস্তারেই বেশি মনোযোগী এবং তার স্বার্থ যে রক্ষা করবে, তাতে সে 'রাম-শ্যাম-যদু-মধু' যেই হোক—আমেরিকা তার পেছনে থাকবে, এটিই স্বাভাবিক।
৩.
বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থও অনেক। কেননা তারাও জানে যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিবেশী বদলানো যায় না। সামাজিক জীবনে প্রতিবেশী বদলানো যায়। ভাড়াটিয়াদের পক্ষে এটা খুবই সহজ। এমনকি কেউ যদি তার প্রতিবেশী বদলাতে চায় তাহলে সে তার নিজের বাড়িঘর বিক্রি করেও অন্যত্র চলে যেতে পারে। কিন্তু একটি রাষ্ট্র চাইলেই তার প্রতিবেশী বদলাতে পারে না। কারণ একটি দেশ চাইলেই আরেকটি দেশের মানচিত্র বদলে দিতে পারে না। সেটা করতে চাইলে যুদ্ধ হবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে সব রাষ্ট্রের জন্যই সেটি ক্ষতিকর।
বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে ভারতের অর্থনীতি, বিশেষ মেডিকেল ট্যুরিজমের যে কী বেহাল দশা হয়, তা গত ৫ আগস্টের পর থেকে তারা টের পাচ্ছে। সম্পর্ক অবনতির কারণে ভারত ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশিদের ভিসাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। জরুরি মেডিকেল প্রয়োজন এবং সরকারি সফর ছাড়া আর কাউকে সেভাবে ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। তাতে যে শুধু বাংলাদেশেরই ক্ষতি হচ্ছে তা নয়। বরং ক্ষতিটা ভারতেরও। তার অর্থনীতির একটি বড় জায়গাজুড়ে আছে মেডিকেল ও পর্যটন—যেখানে বাংলাদেশির অবদান অনেক। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে।
যেকোনো দেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে, তা নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, জনগণের মনোজগত, সরকারপ্রধানদের পারসেপশন বা পূর্বধারণা ইত্যাদি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের যে প্রকৃতি ছিল, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে সেই একই প্রকৃতি ছিল না। আবার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের আগে যে প্রকৃতি ছিল, ১৫ আগস্টের পর সেই চিত্র একেবারেই বদলে যায়। আবার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের পরপর তিনটি এবং চতুর্থ মেয়াদের কিছুটা সময় পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা নিয়ে অনেক আলোচনা যেমন আছে, সেরকম বিতর্কও কম নয়। ফলে ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের পরে দুই দেশের সম্পর্কের চরম অবনতি হয়।
সম্পর্ক কখনো একতরফা হয় না। ভারত এখন আর কেবল নিজের রাষ্ট্র নিয়ে ভাবে না। বরং তার ভাবনায় এখন পুরো এশিয়া এবং সেখানে তার সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী চীন-পাকিস্তান-মিয়ানমার। কিন্তু ভবিষ্যতের 'সম্ভাব্য ব্যাটল গ্রাউন্ড' যে বঙ্গোপসাগর, তার তীরবর্তী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা ভারতের জন্যও জরুরি। অতএব বোঝাপড়াটা এখানেই যে, ভারত এখান থেকে যা নেবে বা নিতে চায়, তার বিনিময়ে সে বাংলাদেশকে কী দিচ্ছে বা দেবে। সেই বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈরিতে মোদির বিলম্বিত শুভেচ্ছাবার্তা একটি শুভসূচনা হতে পারে।







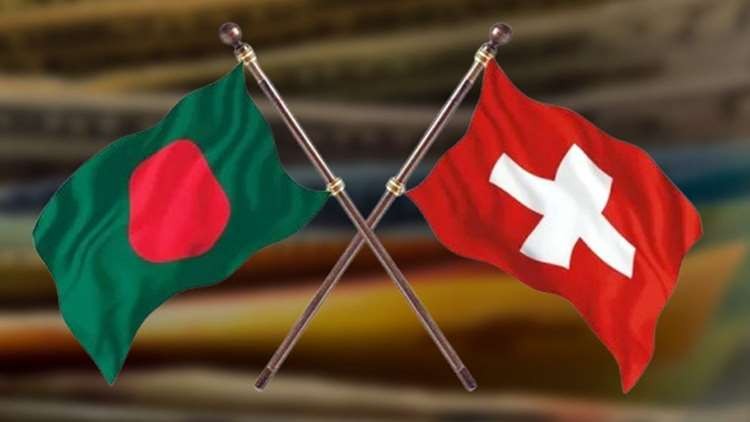











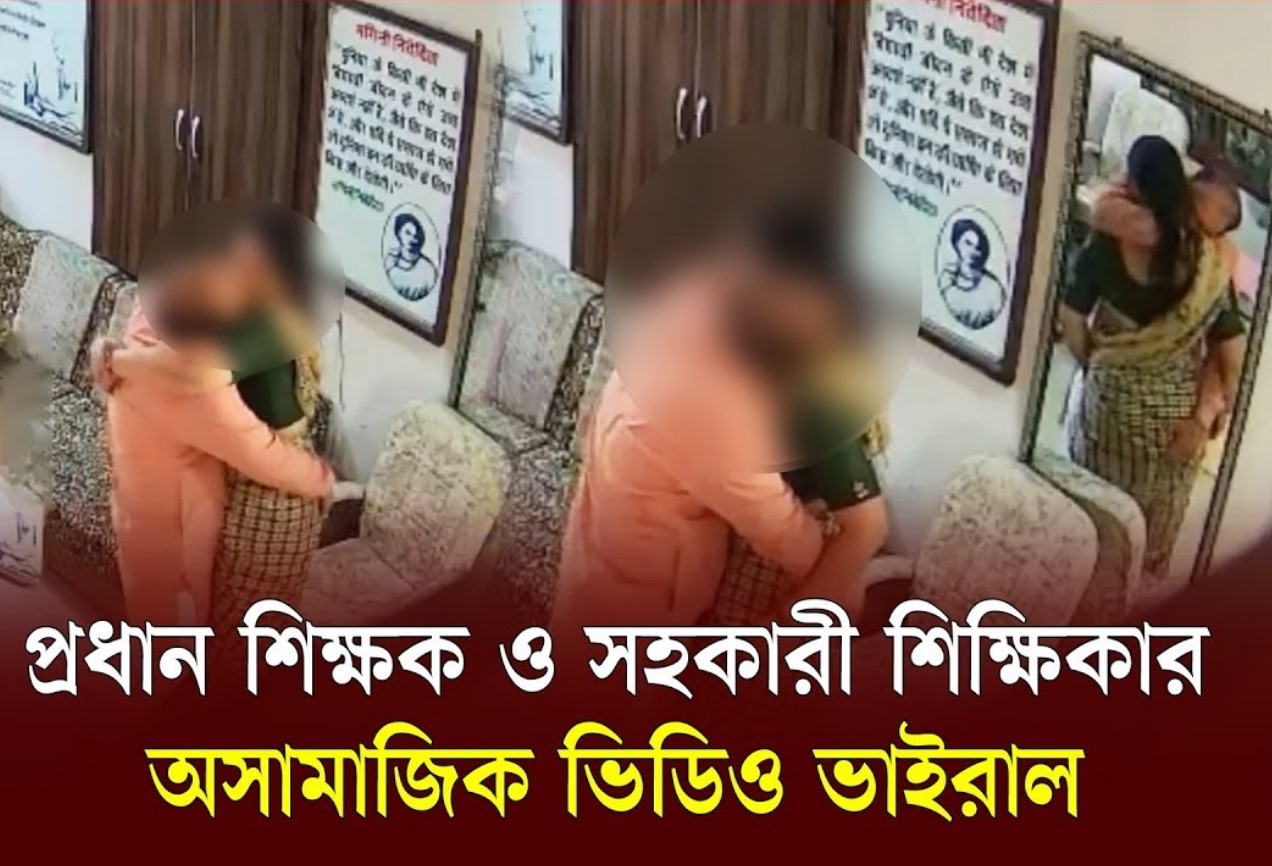








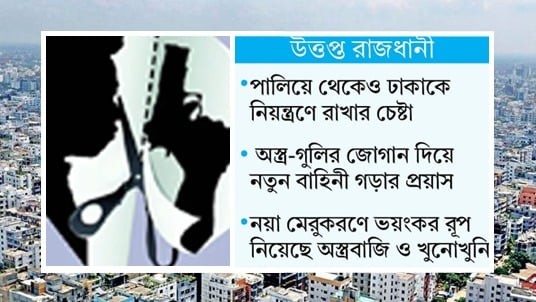



আপনার মতামত লিখুন :